অতিমারী এবং বিভেদের সংস্কৃতি । অমিতাংশু আচার্য
0 356
বিশ্বজুড়ে করোনা অতিমারীর প্রেক্ষিতে নানা রচনার অনুবাদ নিয়ে আমাদের অনুবাদ সিরিজের পঞ্চম কিস্তি ৩ এপ্রিল ২০২০ দ্য হিন্দু প্রকাশিত অমিতাংশু আচার্য-র প্রবন্ধ 'প্যানডেমিকস এন্ড প্রেজুডিস: হোয়েন দেয়ার ইজ এন এপিডেমিক, সোশ্যাল প্রেজুডিসেস রিসারফেস'। 'এখন আলাপ ব্লগ'-এ প্রকাশিত বাংলা অনুবাদটি করেছেন সীমান্ত গুহঠাকুরতা।
**
অতিমারীর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে জৈবিক সহাবস্থান, সমাজে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত চিত্র দেখা যায়। অসুখ কখনো সামাজিক বাছ-বিচার করে হয় না, জীবাণু কখনোই আশ্রয়স্থলকে জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ বা অন্য কোনো পরিচিতি দিয়ে বিচার করে না। যদিও ইতিহাসে বারবার এটা দেখা গেছে যে, যখনই কোনো অতিমারী ঘটেছে, সমাজের গভীরে প্রোথিত বিভেদের সংস্কারগুলো কুৎসিতভাবে বেআব্রু হয়ে পড়েছে এবং তার ফল হয়েছে মারাত্মক।
**
বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডের উচ্চবিত্ত জনবসতিগুলোতে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সেখানকার বাসিন্দাদের অনেকেই খুব রহস্যজনকভাবে টাইফয়েডে আক্রান্ত হতে লাগলেন। দারিদ্র্য এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে এমন একটা অসুখকে এহেন ঝাঁ-চকচকে বিত্তবান মহল্লায় ছড়িয়ে পড়তে দেখে শহরের চিকিৎসক মহল যারপরনাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।
জর্জ সোপার নামের একজন স্যানিটরি ইঞ্জিনিয়ারকে বিষয়টির তদন্তভার দেওয়া হল। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, মেরি ম্যালো নামে একজন মধ্য-বয়স্কা আইরিশ রাঁধুনি টাইফয়েডে আক্রান্ত শেষ আটটি বাড়িতেই রান্নার কাজ করেছেন। নিজে একেবারে সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ম্যালো নামের ওই মহিলা যখন যে বাড়িতে কাজ করেছেন, প্রতিবার সেখানে টাইফয়েড ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারপরই তিনি সেই বাড়ি থেকে কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র কাজ নিয়ে চলে গেছেন। জর্জ সোপার এই মহিলাকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। তিনি সেই মহিলার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করলেন, তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর বাসস্থান খুঁজে বার করলেন এবং অবশেষে সরাসরি তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে টাইফয়েডের বাহক হিসেবে অভিযুক্ত করলেন। ম্যালো তাঁর কথায় কোনো রকম মেডিক্যাল টেস্ট করাতে রাজি হলেন না। অগত্যা সোপারের সুপারিশে পুলিস সেই মহিলাকে গ্রেপ্তার করল।
বিশুদ্ধ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে, ম্যালোর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর রক্ত, মূত্র এবং লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হল। পরীক্ষার ফল এলে তাতে টাইফয়েড সৃষ্টিকারী সালমোলেনা টাইফি নামের ব্যাকটেরিয়াটির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেল। অচিরেই জনতার অসন্তোষ সবেগে আছড়ে পড়ল ম্যালোর ওপর।
এইভাবে জর্জ সোপার প্রথম ‘সুস্থ-বাহক’ (হেলদি ক্যারিয়ার) নামের একদল মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করেন, যারা নিজেরা আক্রান্ত না হয়েও রোগজীবাণু বহন করতে এবং ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। ম্যালো নামের সেই মহিলা ‘টাইফয়েড মারি’ নামে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন।
এই নির্দয় উপাধিটা দশকের পর দশক ধরে একজন দরিদ্র, অশিক্ষিত, উদ্বাস্তু মহিলার প্রতি যাবতীয় হিংস্র এবং অমানবিক আচরণকে বৈধতা দিয়ে গেছে। সেই মহিলা একজন খুবই দরদী এবং দক্ষ রাঁধুনিও ছিলেন। চিকিৎসক-মহল এবং সাংবাদিকেরা ম্যালোকে ‘সুপার স্প্রেডার’ আখ্যা দিয়ে প্রায় ডাইনিতে বা গণ-হত্যাকারীতে পরিণত করেছিল। ধারণা করা হয় যে তার মাধ্যমে একান্ন জন লোক সংক্রমিত হয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল তিনজন, যদিও এই ব্যাপারে সঠিক সংখ্যাটা জানা খুবই কঠিন।
শত্রুকে খুঁজে বার করা
ম্যালোকে ছাব্বিশ বছরের জন্য নর্থ ব্রাদার আইল্যান্ডে, রিভারসাইড হাসপাতালের কাছে কোয়ারান্টাইনে পাঠানো হয়। সেখানেই ১৯৩৮ সালে তিনি মারা যান। এই ঘটনার পাক্কা তেষট্টি বছর পরে একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে খুবই দরদ দিয়ে সেই মহিলার হয়ে জবাবদিহি করলেন একই পেশার অন্য একজন মানুষ। ‘টাইফয়েড মেরি: অ্যান আরবান হিস্টোরিক্যাল’ (২০০১) নামের বইতে অ্যান্থনি বোর্ডেন তাঁরই মত আরেক রাঁধুনি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সমানুভূতি নিয়ে লিখলেন, “রাঁধুনিদের অসুস্থ অবস্থাতেই কাজ করতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজে না গেলে বেতন কাটা যায়। তুমি জল ঝরাতে থাকা নাক এবং বসে যাওয়া গলা নিয়ে জেগে উঠেছ? তা নিয়েই তোমাকে লড়ে যেতে হবে। তোমাকে সময়মত কাজ সারতেই হবে। তুমি গলায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এইভাবে যাবতীয় ব্যথা আর অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে যাওয়াটা আসলে কিন্তু একটা গর্ব করার মতই বিষয়।”
নিউ ইয়র্কে টাইফয়েডের সংক্রমণ মোটেও নতুন কোনো ব্যাপার ছিল না। অথচ ম্যালোকেই একমাত্র গণশত্রু করে তোলা হয়েছিল, বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল রোগটার থেকেও বিপজ্জনক। আসলে তাঁর অপরাধ সম্ভবত এটাই ছিল যে, ধনী এবং ক্ষমতাশালী শ্রেণিটিকে তিনি একথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কোনো রোগ-জীবাণু সেই অর্থনৈতিক ভেদাভেদকে স্বীকার করে না—যে ভেদাভেদ সবসময় লং আইল্যান্ডের থেকে ব্রংক্সকে আলাদা করে রাখে।
**
মধ্যযুগের ইউরোপে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার জন্য দোষ চাপানো হত সেই সমস্ত লোকেদের ঘাড়ে, যারা প্রাচীন ও সাবেকী চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা করতেন। তাদের ‘ডাইনি’ অপবাদ দিয়ে মেরে ফেলা হত।
মানুষ এবং জীবাণুর সম্পর্কের মধ্যে এক জটিল বিবর্তনবাদী সহাবস্থানের গল্প রয়েছে। জীবাণুগুলো বেঁচে থাকতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে চায়। মানুষ হল তাদের আশ্রয়দাতা, কাজেই মানুষকে মেরে ফেললে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি। উভয়েই তাই বেঁচে থাকার জন্য আপোষ করেই যা করার করে। একটা সময় পর তাই দুজনেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে এবং তারপর থেকে মানুষ সেই জীবাণুকে নিয়েই ঘর করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ জিনিস আমরা আগেও বহুবার করেছি এবং নোভেল করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রেও তাই-ই হতে চলেছে।
অতিমারীর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে জৈবিক সহাবস্থান, সমাজে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত চিত্র দেখা যায়। অসুখ কখনো সামাজিক বাছ-বিচার করে হয় না, জীবাণু কখনোই আশ্রয়স্থলকে জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ বা অন্য কোনো পরিচিতি দিয়ে বিচার করে না। যদিও ইতিহাসে বারবার এটা দেখা গেছে যে, যখনই কোনো অতিমারী ঘটেছে, সমাজের গভীরে প্রোথিত বিভেদের সংস্কারগুলো কুৎসিতভাবে বেআব্রু হয়ে পড়েছে এবং তার ফল হয়েছে মারাত্মক।
১৩৪৮ সালের ইউরোপে যখন ‘গ্রেট বিউবোনিক প্লেগ’ ছড়িয়ে পড়েছিল, ক্যাথলিক চার্চ এই মর্মে নিশ্চিত ছিল যে এই ‘ব্ল্যাক ডেথ’ আসলে খ্রিস্টধর্মকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদিদের একটা অন্তর্ঘাত। কুয়োর জলে গোপনে বিষ মিশিয়ে রোগ ছড়ানোর অপবাদ দিয়ে সেসময় ইহুদিদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হত, তাদের কাছ থেকে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হত। অচিরেই হাজার হাজার ইহুদির দেহের মাংস-পোড়া গন্ধ স্ট্র্যাসবুর্গ, কোলন, বেজে়ল আর মেইনৎস ইত্যাদি শহরগুলোর আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল।
ইউরোপের জিপসিদেরও একই রকম নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছিল। জর্জ্জিও ভিয়াজ্জিও তাঁর ‘স্টোরিয়া ডেগলি জিঙ্গারি ইন ইটালিয়া’ (১৯৯৭) বইতে ১৪৯৩ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে বলবৎ হওয়া এমন একশো একুশটা আইনের উল্লেখ করেছেন যেগুলো দেশের অভ্যন্তরে জিঙ্গারি তথা জিপসিদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই তৈরি হয়েছিল। এই আইনগুলো আনা হয়েছিল অংশত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে জিপসিদের মারফতই মহামারী সৃষ্টি হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে।
মধ্যযুগের ইউরোপে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার জন্য দোষ চাপানো হত সেই সমস্ত লোকেদের ঘাড়ে, যারা প্রাচীন ও সাবেকী চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা করতেন। তাদের ‘ডাইনি’ অপবাদ দিয়ে মেরে ফেলা হত। ঐতিহাসিক ব্রায়ান লেভ্যাকের (২০০৬) হিসেব অনুযায়ী সেই সময় ইউরোপে প্রায় নব্বই হাজার লোককে ডাকিনীবিদ্যা চর্চার অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। বোঝাই যায়, এর বেশিরভাগটাই ভোগ করতে হয়েছিল মহিলাদের।
**
প্রচার করা হয়েছিল যে, বিশেষ করে উপনিবেশের বাসিন্দাদের ‘ইন্টেস্টাইন’ আর ‘বিলিয়ারি ট্র্যাক্টেই’ নাকি ওই জীবাণুর দেখা মেলে।
‘প্লেগ স্প্রেডার’ সম্পর্কিত এই যে মধ্যযুগীয় ধারণা, জীবাণুর আবিষ্কার এসে তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। তখনই প্রথম জানা গিয়েছিল যে, রোগ মানুষের মাধ্যমে ছড়ায় না, ছড়ায় কিছু আণুবীক্ষণীক প্রাণী এবং জীবাণুর মাধ্যমে। এই জীবাণু জল, বাতাস বা মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর শারীরিক সংযোগের মাধ্যমেও বাহিত হতে পারে। বলা যেতে পারে যে, এতদিন যে মহামারীকে দেখা হত সামাজিক সংস্কারের বিকৃত চশমা দিয়ে, আদ্যন্ত ‘অরাজনৈতিক’ এবং ‘নীতি-নিরপেক্ষ’ জীবাণুর আবিষ্কার এসে সেই মহামারীকে মাইক্রোস্কোপের লেন্সের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে দেখতে শেখাল।
কিন্তু নিছক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত এই মাইক্রোস্কোপও অচিরেই সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের অস্ত্র হয়ে উঠল। ক্রান্তীয় জলবায়ু-অঞ্চলগুলো নানাবিধ অসুখে বোঝাই হয়ে থাকত, যা সেখানকার অ্যাংলো-ইউরোপীয়ান শাসকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেকটাই ক্ষতিকর ছিল। উপনিবেশের প্রজাদের তুলনায় মশারা তাদের কাছে অনেক বেশি বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতএব মাইক্রোস্কোপ এসে ‘ট্রপিক্যাল ডিজিজ’ নামে একটা ঔপনিবেশিক ধারণাকে তৈরি করে দিল। যেমন ১৮১৭ সালে ছড়িয়ে পড়া অতিমারীটির নাম দেওয়া হল ‘এশিয়াটিক কলেরা’, কারণ ধারণা করা হয়েছিল যে, এই রোগটির উৎপত্তি ভারতীয় গাঙ্গেয় অঞ্চল থেকে। এই কলেরা খুব দ্রুত ইউরোপ মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং উপনিবেশগুলো থেকে এরকম আরও রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় সেখানকার লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
অতি দ্রুত নিবিড় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞান কীভাবে ব্যাধিগুলিকে নির্দিষ্ট এলাকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করত, তার খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ঐতিহাসিক প্রতীক চক্রবর্তী। ২০১০ সালে প্রকাশিত একটা লেখায় তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে রবার্ট কখ্-এর আবিষ্কার ভিব্রিও কলেরাই নামের কমার আকৃতির জীবাণুটিকে ক্রান্তীয় জলবায়ুতে এবং সেখানকার মানুষজনের শরীরে উৎপন্ন বলে দেগে দেওয়া হয়েছিল। এও প্রচার করা হয়েছিল যে, বিশেষ করে উপনিবেশের বাসিন্দাদের ‘ইন্টেস্টাইন’ আর ‘বিলিয়ারি ট্র্যাক্টেই’ নাকি ওই জীবাণুর দেখা মেলে।
তারপর এল কুষ্ঠ। এই রোগটির ব্যাপারে সামাজিক সংস্কার এতটাই তীব্র যে, রোগের নামটাই যেন সামাজিক বহিষ্কারের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। মনুস্মৃতিতে কুষ্ঠরোগীদের ‘পাপী’ হিসেবে বর্ণনা করে তাদের সমাজ থেকে ‘একঘরে’ করে দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছিল। ১৮৯১ সালে ‘লেপ্রসি কমিশন’-এর রিপোর্টে কুষ্ঠরোগকে ‘এতটাই কম সংক্রামক যে তাকে গুরুত্ব না দিলেও চলে’ বলে ঘোষণা করা হলেও, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উচ্চবিত্ত সমাজ কুষ্ঠরোগীদের প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে অনুমতি দেওয়ার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যায়, যেহেতু তাদের চেহারা বিরক্তি এবং ঘৃণার উদ্রেক করে। এরই ফলে ১৮৯৮ সালে বিধিবদ্ধ হয় ‘লেপ্রসি অ্যাক্ট’, যা কুষ্ঠরোগীদের একেবারেই অন্তরীণ করে ফেলে, এমনকী তাদের লিঙ্গ-অনুযায়ী পৃথক থাকতে বাধ্য করা হত, যাতে তারা বংশবৃদ্ধি করতে না পারে। পুরোটাই করা হয়েছিল উপনিবেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের নান্দনিক চেতনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য।
উপনিবেশবাদী বিজ্ঞান যদি মহামারীর এহেন ‘ক্রান্তীয়-করণে’ সাহায্য করে, সাহিত্য সেই ধারণাকে আরও মজবুত করেছে। থমাস মানের উপন্যাস ‘ডেথ ইন ভেনিস’-এর পটভূমি ছিল কলেরা আক্রান্ত ‘সিটি অফ ওয়াটার’ ভেনিস। সেখানে তিনি রোগটাকে ‘ইন্ডিয়ান কলেরা’ হিসেবেই বর্ণনা করেছেন, যা নাকি “গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের উষ্ণ ও আর্দ্র জলাভূমিগুলোতে তৈরি হয়। সেই পরিত্যক্ত অস্বাস্থ্যকর জলাভূমিগুলো থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়, যেখানে কোনো মানুষ ভুলেও পা রাখে না।”
মহামারীর প্রাচ্যীকরণ
গবেষক আলেকজান্ডার হোয়াইট ২০১৮ সালে তার গবেষণাপত্রে এই জাতীয় ঔপনিবেশিক নির্মিতিকে ‘মহামারীর প্রাচ্যীকরণ’ (এপিডেমিক ওরিয়েন্টালিজম) বলে অভিহিত করেছেন। রোগের নামগুলো দেখলেই এই পদ্ধতিটা বোঝা যায়। যেমন এশিয়াটিক কলেরা (১৮২৬), এশিয়াটিক প্লেগ (১৮৪৬), এশিয়াটিক ফ্লু (১৯৫৬), রিফট্ ভ্যালি ফিভার (উনিশ শতক), মিডল ইস্ট রেসপিরেটোরি সিনড্রোম (২০১২), হংকং ফ্লু (১৯৬৮) ইত্যাদি। এখন অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আচরণবিধি অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে, ‘জেনেরিক টার্ম’ ব্যবহার করেই রোগের নামকরণ হয়।
সামাজিকভাবে অবশ্য এখনো মহামারী এবং নানা রোগব্যাধিকে জাতি, লিঙ্গ, যৌন নির্বাচন এবং ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিকভাবে দেগে দেবার চল রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন বারবার কোভিড-১৯-কে ‘চাইনিজ ভাইরাস’ বলে অভিহিত করেছে, এবং অনেকে বিদ্রুপ করে এটিকে ‘কুং ফ্লু’ বলেও ডাকছে। এই জাতীয় নামকরণ কুসংস্কারগুলোকে পোক্ত করে। এইচ আই ভি বা এইডসকে আড়ালে GRID নামে ডাকা হত, যা ছিল গে রিলেটেড ইমিউনোডেফিশিয়েনসি-র সংক্ষিপ্ত রূপ। খুব অল্প সময় স্থায়ী হলেও এই নামটি সেই ধারণাকেই তোল্লাই দেয়, যা আশির দশকে আগ্রাসী আমেরিকান মিডিয়া প্রচার করেছিল। তারা এই রোগটিকে ‘গে-প্লেগ’ হিসেবে অভিহিত করেছিল, যেন তা যৌন-বিকৃতির ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তি। এইচ আই ভি/এইডস বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সমকামী পুরুষদেরই হয়ে থাকে—অনেক রাষ্ট্রই এখনো এরকম একটা উদ্ভট ধারণা পোষণ করে। শুধু তাই নয়, সেই সমস্ত দেশে সমকামী পুরুষদের রক্তদান বা অঙ্গদানও নিষিদ্ধ।
**
যে সরকার বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ঘরে ফেরানোর জন্য বিশেষ বিমান চালাতে পেরেছে, সেই সরকারই তার দরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদে তাদের ঘরে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।
ইতিহাস আমাদের একটা জিনিস স্পষ্ট করে দিয়েছে। তা হল এই যে, আমরা রোগব্যাধি সৃষ্টিকারী জীবাণুদের খুব সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করতে পারলেও বৈষম্যমূলক সংস্কারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। অতিমারী ঘৃণা তৈরি করে না, কিন্তু তাকে বাড়িয়ে তুলতে অবশ্যই সাহায্য করে।
ট্রাম্প প্রশাসন এটা বিশ্বাস করতে ভালবাসে যে চীনা প্রশাসনের অব্যবস্থা, ঘটনাকে ধামাচাপ দেওয়ার চেষ্টা এবং কোভিড-১৯ এর ছড়িয়ে পড়া—সবটাই আসলে আমেরিকাকে ব্যতিব্যস্ত করার চক্রান্ত। এটা দেখে ক্যাথলিক চার্চ প্রচারিত সেই মিথ্যাটার কথা মনে পড়ে যায় যে, ইহুদিরা নাকি খ্রিস্টধর্মকে ধ্বংস করার জন্য চক্রান্ত করে রোগ ছড়িয়ে দিত। একই রকম ভাবে, ইউরোপীয়ান রাজনীতিবিদ লি পেন এবং সালভিনি যখন উদ্বাস্তু এবং শরণার্থীদের করোনা ভাইরাসের বাহক বলে জাতিবিদ্বেষী অপপ্রচার চালান, তখন তা ট্রাম্পের উগ্র ভাষ্যের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায়। বছর চারেক আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারপর্বে ট্রাম্প ‘প্লেগ স্প্রেডার’ সংক্রান্ত সেই মধ্যযুগীয় ধারণার পুনরাবৃত্তি করে দাবি করেছিলেন, মেক্সিকান শরণার্থীরা নাকি ‘সীমান্ত পার করে ভয়ঙ্কর সব সংক্রামক রোগ ঢেলে দিচ্ছে।’ মজার ব্যাপার হল, সেই মেস্কিকোই এখন তার সীমান্ত প্রহরা দিচ্ছে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে করোনা ভাইরাসের বাহকরা সেদেশে ঢুকে না পড়তে পারে।
ভারতেও নানা রকম সুপ্ত বিভেদকামী ধ্যানধারণা কোভিড-১৯ এর সঙ্গে তাল রেখে দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ফ্ল্যাটের মালিকরা চিকিৎসা-কর্মীদের তাঁদের নিজেদের বাসস্থানে ঢুকতে বাধা দিয়েছেন। সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করার অজুহাতে মানুষ জাতপাত আর অস্পৃশ্যতা-বাচক নানা শব্দ ব্যবহার করছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের প্রতি নানা রকম জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য করা হচ্ছে এবং তাদের উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যে সরকার বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ঘরে ফেরানোর জন্য বিশেষ বিমান চালাতে পেরেছে, সেই সরকারই তার দরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদে তাদের ঘরে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই লকডাউন শ্রমিকদের এক বিরাট মিছিল দেখেছে, যারা বাড়ি ফেরার জন্য কয়েকশো মাইল পথ হেঁটেছে, ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে, খাবার আর জলের জন্য হাহাকার করেছে। এখনও পর্যন্ত কুড়ি জন এমন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হবার পর সরকার অবশ্য যে সমস্ত শ্রমিক থেকে যেতে চায় তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করে কিছু আশ্রয়-শিবির তৈরি করেছে, আর যারা বাড়ি ফিরতে চায় তাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করছে। আবার উত্তরপ্রদেশে ঘরে ফিরতে থাকা শ্রমিকদের ওপর এমনভাবে জীবাণুনাশক ছড়ানো হয়েছে, যেন তারা প্রত্যেকেই এক একটা জীবন্ত ভাইরাস। এর সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লির নিজামুদ্দীন এলাকায় তবলিঘি জামাতের সমাবেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।
**
বিজ্ঞানের কাজ হল এই জাতীয় যুক্তিহীন বিশ্বাসগুলো থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করা। কারণ বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করেছে যে জীবাণু জাতপাত বা ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে সংক্রমণ ঘটায় না, তার দরকার শুধুমাত্র একটি উষ্ণ-আর্দ্র এবং তার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যে ভরপুর একটি মানব-শরীর। কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, রোগের আশ্রয়দাতা শরীর, রোগের সঞ্চারক এবং বাহক সংক্রান্ত বিজ্ঞাননির্ভর সত্যগুলোকেও সামাজিক বিভেদ বাড়িয়ে তোলার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
অতিমারীর আবহে তৈরি হওয়া ভ্রান্ত সংস্কার সমাজের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ম্যারি ম্যালোর মত করে নিজের জীবন দিয়ে তা আর কেউ বোঝেনি। জীবনের এক চতুর্থাংশ সময় কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরও তার শাপমুক্তি ঘটেনি। আজ পর্যন্ত তাঁর নামটি রোগের সমার্থক হয়ে থেকে গেছে।
রোগাক্রান্তদের প্রতি সেই একই রকম আগ্রাসী মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে আজও। কোয়ারান্টাইন বিধি কঠোরভাবে বলবত করার অজুহাতে সরকার রোগীর নাম ঠিকানা প্রকাশ্যে এনে ফেলছে, তাদের দরজায় পোস্টার মারছে, তাদের দেহে অমোচনীয় কালিতে স্ট্যাম্প মেরে দিচ্ছে। এ সবই চিকিৎসা সংক্রান্ত নৈতিক বিধিগুলির বিরোধী এবং এগুলি সামাজিক বহিষ্কারের দিকে মানুষকে ঠেলে দিতে পারে।
বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একজন দরিদ্র উদ্বাস্তু মহিলা সমাজের দিকে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, আজ আবার সেই একই প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি আমরা—মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মানবিকতা বিসর্জন দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে কি?
মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি ‘দ্য হিন্দু’ কাগজে ৩ রা এপ্রিল ২০২০-তে প্রকাশিত হয়।
অনুবাদ : সীমান্ত গূহঠাকুরতা

Tagsadolescence age of consent age of marriage caa child marriage corona and nursing covid19 Covid impacts on education domestic violence early marriage education during lockdown foremothers gender discrimination gender identity gender in school honour killing human rights intercommunity marriage interfaith marriage lockdown lockdown and economy lockdown and school education lockdown in india lockdown in school lockdown in schools love jihad marriage and legitimacy memoir of a nurse misogyny nrc nurse in bengal nursing nursing and gender discrimination nursing in bengal nursing in india online class online classes during lockdown online education right to choose partner school education during lockdown social taboo toxic masculinity transgender Women womens rights
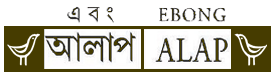
Leave a Reply