একজন প্রিভিলেজড মুসলিম মেয়ের কথা
0 125
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ছাত্রী নাজনিন (নাম পরিবর্তিত)। আর্থ-সামাজিকভাবে সে যে সুবিধাভোগী শ্রেণির, তা সে স্বীকার করে। কিন্তু নাজনিন নিজে সংখ্যালঘু। তার উপর সিএএ বিরোধী আন্দোলনেও যুক্ত। তার সাক্ষাৎকার নিলেন শতাব্দী দাশ৷ মাথায় রাখতে হবে, নাজনিন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতা। গণতন্ত্রে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার তার আছে। তা সত্ত্বেও এবং নিজের আর্থ-সামাজিক প্রিভিলেজ সত্ত্বেও, তাকে নিজের আসল নাম গোপন রাখার জন্য অনুরোধ করতে হয়!
শতাব্দী: নিজের সম্পর্কে কিছু বলো। তুমি, তোমার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড...
নাজনিন: আমি যথেষ্ট প্রিভিলেজড একজন মানুষ। আমার বাবা সরকারি চাকুরে, বেশ উঁচু পদেই আছেন। মা হোম মেকার। আমাদের সাথে আমার নানি থাকেন। তিনি আমার মায়ের মা । আমাদের, মানে আমায় আর আমার দিদিকে, উনিই ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন। আমার লেখাপড়ায় হাতেখড়িও ওনার কাছেই। আমার দিদি পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে যোগ দিয়েছে৷ আর আমি পড়ছি এখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট। আমরা সল্টলেকের একটি আবাসনে থাকি।
শতাব্দী: তোমার পূর্বজদের আদি বাসস্থান কোথায়? সেটা তো সল্টলেকে নয়। এপার বাংলায়, না ওপার বাংলায়? কী কারণে কবে মাইগ্রেট করা হয়?
নাজনিন: আমার মায়ের পুরো পরিবার কলকাতায় সেটলড হলেও, তাঁদের আদি বাড়ি বীরভূম। শান্তিনিকেতন থেকে একটু দূরে। বাবার পরিবারও এপার বাংলার। উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে তাঁদের বাড়ি এখনও। তাই মাইগ্রেট করা হয়ত বলা যায় না৷ পড়াশোনা ও চাকরির প্রয়োজনে আস্তে আস্তে তাঁরা শহরমুখী হন৷
শতাব্দী: এখন যেখানে থাকো, সেটা একটা হিন্দু মেজরিটি অঞ্চল। সেখানে বাজার হাট থেকে শুরু করে সামাজিক মেলামেশায় কোনো সমস্যা কি আগে হয়েছে? কোনো রকম তীর্যক দৃষ্টি বা ‘আদারাইজেশন’ দেখেছ?
নাজনিন: যেখানে থাকি সেখানে আলাদা করে অন্তত বাঙালিদের মধ্যে কোনো বৈরী ভাব দেখিনি। পাবলিকলি তো না বটেই। নিজেদের মধ্যে মুসলিমদের প্রতি কোনো বিদ্বেষমূলক কথা বলেন কিনা, আমার জানা নেই৷ কিন্তু অন্তত আমাদের সামনে বলেন না৷ সেটা আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থানের জন্যও হতে পারে। বরং অবাঙালি অনেকেই পাবলিকলিই তাঁদের স্ট্যান্ডপয়েন্ট বলে থাকেন। মানে ধর্ম নিয়ে একটু হলেও বেশি মাতামাতি আমি তাঁদের মধ্যে দেখেছি। তবে আমাদের দিকে আলাদা করে তীর্যক কোন দৃষ্টি অথবা একেবারে আলাদা করে দেওয়া, এরকম চরম কিছু আমি কখনও ফেস করিনি। ছোটবেলা থেকে একই আবাসনে আছি। একই মানুষজনের সাথে খেলাধুলা করে বড় হয়েছি। বন্ধুত্ব বা প্রায় আত্মীয়তার সম্পর্ক তাদের সঙ্গে। কোনোদিনও অন্যকিছুর মুখোমুখি হতে হয় নি আমায়। ফরচুনেটলি।
আসলে এটা সমাজের একটা প্রতিফলন। একটি কমিউনিটি কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে এটা তারই লক্ষণ মাত্র। আমাদের কমিউনিটির মেয়েরা কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে আছে। এর একটা কারণ হতে পারে এই যে তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল৷ তারা সংখ্যালঘু তো বটেই, পুরুষমানুষের প্রিভিলেজও তাদের ছিল না
শতাব্দী: তুমি একটি এলিট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়। সেখানে কত পার্সেন্ট মুসলিম আছেন তোমার ডিপার্টমেন্টে বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে? কম হলে সংখ্যাটা এত কম কেন হল? কী মনে হয়?
নাজনিন: আমার ডিপার্টমেন্টে খুব বেশি সংখ্যক মুসলিম নেই। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও নেই। পুরুষ প্রায় নেই। মহিলা তাও আছেন। আসলে এটা সমাজের একটা প্রতিফলন। একটি কমিউনিটি কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে এটা তারই লক্ষণ মাত্র। আমাদের কমিউনিটির মেয়েরা কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে আছে। এর একটা কারণ হতে পারে এই যে তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল৷ তারা সংখ্যালঘু তো বটেই, পুরুষমানুষের প্রিভিলেজও তাদের ছিল না। একসময় তাই তারা বুঝতে শুরু করেছে যে শিক্ষা ছাড়া গতি নেই, উন্নতির কোনো পথ নেই।
শতাব্দী: সিএএ এনআরসি-র পর বাড়ির বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে, কমবয়সীদের মধ্যে এবং আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কীরকম উদ্বেগ দেখেছ?
নাজনিন: অসম এনআরসি-র পর সত্যিই বাড়িতে ভীতি দেখা গেল। এতজন মানুষ বাদ পড়লেন! সবাই অনুপ্রবেশকারী? মনে তো হয় না৷ বাড়িতে একটি সাময়িক উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। নানীর চিন্তা হচ্ছিল যে তিনি কিভাবে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করবেন। অনেক খোঁজ করে একটি পুরনো জমির দলিল পাওয়া গেল যাতে নানীর নাম আছে। ফলে সম্ভবত অত চিন্তা আর নেই। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে হালকা হলেও চিন্তা আছে। আমাদের কিছু আত্মীয় আছেন যাঁরা কিছুকাল বিদেশে ছিলেন, আবার ফেরত এসেছেন৷ বিশেষত তাঁদের মধ্যে বেশ উদ্বেগ দেখছি। মাঝে মাঝেই কথাবার্তা চলছে—কী কাগজ লাগবে তাই নিয়ে। তারপর এল ক্যাব (CAB), যা এখন আইন হয়ে গেছে—সিএএ। এই আইন স্পষ্টতই বৈষম্যমূলক৷ তা নিয়ে অসন্তোষও দেখছি তাঁদের মধ্যে৷
অসম এনআরসি-র পর সত্যিই বাড়িতে ভীতি দেখা গেল। এতজন মানুষ বাদ পড়লেন! সবাই অনুপ্রবেশকারী? মনে তো হয় না৷ বাড়িতে একটি সাময়িক উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। নানীর চিন্তা হচ্ছিল যে তিনি কিভাবে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করবেন। অনেক খোঁজ করে একটি পুরনো জমির দলিল পাওয়া গেল যাতে নানীর নাম আছে।
শতাব্দী: আচ্ছা তোমাদের বাড়ির কাজের মহিলা? তিনি কী বলছেন এ বিষয়ে?
নাজনিন: আমাদের বাড়িতে যিনি কাজ করেন, তিনি থাকেন সুন্দরবনে। এখানে কাজের সন্ধানে এসে পড়েছেন। তিনি আমার মাকে একদিন বলেছিলেন, "বৌদি, এত এনআরসি করে কী লাভ? মানুষগুলো যারা মধু আনতে গিয়ে মারা যায়, বা আমাদের সুন্দরবনের গ্রামে যেখানে আলো নেই, সেই জায়গাগুলোর, সেই মানুষগুলোর উন্নয়ন করলেই তো পারে।" এই কথা আমায় খুব ভাবিয়েছিল। এভাবেই এই দেশের সরকার বড় ইস্যুগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছোট বিষয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছে। এনআরসি হলে, হওয়ার পর কী হবে জানিনা৷ কিন্তু এনআরসি হবে হবে এই গুজবে কেউ এই প্রশ্ন করছে না যে খাবারের দাম বেশি কেন, বা চাকরি নেই কেন।
শতাব্দী: তোমার আর্থসামাজিক শ্রেণি তোমাকে এই ক্রাইসিসে বাঁচিয়ে দেবে বললে। কী কী ভাবে এখানে এই ‘ক্লাস’টা ফ্যাক্টর হল?
নাজনিন: আমার পূর্বপুরুষরা শিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের জমি কেনার মত ক্যাপিটাল ছিল। যারা গরীব, তারা কোনোদিনও জমি কিনতে পারেনি। তাই তাদের পার্টিনেন্ট নথি নেই। তাই তারা হয়ে যাবে অনুপ্রবেশকারী। সবাই নাকি আবার অনুপ্রবেশকারীও হবে না৷ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈনরা হবে শরণার্থী৷ মুসলিমরা হবে অনুপ্রবেশকারী।
শতাব্দী: তাহলে যারা গরীব এবং মুসলিম এবং মহিলা তাদের অবস্থা কীরকম হতে পারে বলে মনে করছ?
নাজনিন: অসমের মতো এখানেও তাঁদের অবস্থা বেশ খারাপই হবে বলে মনে হয়৷ তার সাথে এটাও দেখতে হবে যে বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে নিষিদ্ধ হলেও অনেকেই তাঁদের মেয়েদের ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে দিতেন। আঠেরো পূর্ণ হওয়ার আগেই। তাই ভোটার তালিকা অনুযায়ী তার পাশে নাম থাকে তার স্বামীর, বাবার না। এভাবে সে কোন লিংক দিতে পারেনা তার বাবার সাথে তার সম্পর্ক প্রমাণের। এদিকে সবাই আমার নানীর মতো ভাগ্যবতীও নন। বিশেষত মেয়েদের নামে কি আর জমিজায়গা থাকে? তাঁদের স্কুলের ডিগ্রির শংসাপত্রও থাকে না অনেক ক্ষেত্রে। অবশ্যই মেয়েরা প্রান্তিকদের মধ্যেও বেশি প্রান্তিক।
শতাব্দী: এনআরসি সিএএ নিয়ে হিন্দু প্রতিবেশীরা কী বলছেন? এটা কি কোনোভাবে মুসলিম ব্যাশিং বাড়িয়ে দিল?
নাজনিন: না৷ আমার প্রতিবেশীরা সবাই এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ করেছেন। কোনোভাবেই আমায় খারাপ কিছু ফেস করতে হয় নি। কিন্তু ওই যে বললাম, আমার আর্থ-সামাজিক অবস্থানটা অবশ্যই ম্যাটার করে।
শতাব্দী: যাদবপুরের আন্দোলন সম্পর্কে কী মত? রাজ্যপালকে ঢুকতে না দেওয়া বা তাঁকে "বহিষ্কার" করে খোলা চিঠি নিয়ে কী মত?
নাজনিন: যাদবপুরের আন্দোলন এবং দেশ জুড়ে যে ছাত্র আন্দোলন চলছে, তা থেকে একটাই জিনিস পরিষ্কার—ছাত্ররা এই দেশের পরিস্থিতি এবং তার পরিণতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ছাত্ররাই আশার আলো। ছাত্ররাই জাতি-ধর্ম না দেখে একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়ে পড়তে সবসময় প্রস্তুত।
ওই যে বললাম, আমার আর্থ-সামাজিক অবস্থানটা অবশ্যই ম্যাটার করে।
শতাব্দী: এই আন্দোলন ইন্টারসেকশনাল হতে পারছে? যাদবপুরে তোমার যে কমরেডরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে মুসলিম কারা আছেন?
নাজনিন: অনেকেই মুসলিম আছেন। তবে আমার মতে আন্দোলন এখন কেবলমাত্র মুসলিমদের অধিকার রক্ষায় সীমাবদ্ধ নেই। এখানে সাংবিধানিক অধিকার যে লঙ্ঘন হচ্ছে, তার প্রতিবাদ এবং এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্যেও প্রতিবাদ। জেএনইউতে ফি নিয়ে আন্দোলনের সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল সবার রাইট টু এডুকেশন, অর্থাৎ শিক্ষার অধিকার বাঁচিয়ে রাখা। একজন ভাগচাষীর পক্ষে প্রতিমাসে সাত হাজার টাকা তার ছেলে বা মেয়ের পড়াশোনার খাতে খরচ করা সম্ভব না। পভার্টি লাইন এবং তার সাথে সম্পর্কিত রাজনীতির কথা আমরা সবাই জানি। একইভাবে সংবিধান যেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে সমানাধিকার দিয়েছে, তখন সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে গেলে বৈষম্যের নীতি বা বৈষম্যমূলক কোনো আইন চাপিয়ে দেওয়া চলে না৷ মেনে নেওয়াও চলে না৷
মুসলিম হিসেবে নয় শুধু, তরুণ প্রজন্ম হিসেবে৷ কবে লড়াই থামবে জানিনা৷ শুধু জানি, পিছিয়ে আসার আর পথ নেই
শতাব্দী: পার্ক সার্কাসের মহিলাদের আন্দোলন দেখে কেমন লাগছে?
নাজনিন: দরিদ্র মুসলিম পরিবারের মেয়েরা যেভাবে সাহস নিয়ে পথে বসলেন, তাতে আমি অভিভূত৷ মনে রাখতে হবে, এদের অনেক পরিবারে পর্দাপ্রথা এখনও চলে। আমি মুসলিম, কিন্তু এমনকী আমার অবস্থান থেকেও এই সাহসটা পরিমাপ করা সম্ভব নয়৷ আমি মুক্তমনা পরিবারে বড় হয়েছি। এঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, এঁরা কিন্তু অনেকেই কাল পর্যন্ত বাইরে বেরোতে সংকোচ বোধ করতেন৷ কতটা অসহায় অবস্থা হলে, কতটা ভয় পেলে, এরকম মহিলারা বাইরে বেরিয়ে আসে!
নাজনিন: এঁদের আন্দোলন কোথায় থামবে মনে হয়?
জানিনা। আমরা পাশে আছি৷ মুসলিম হিসেবে নয় শুধু, তরুণ প্রজন্ম হিসেবে৷ কবে লড়াই থামবে জানিনা৷ শুধু জানি, পিছিয়ে আসার আর পথ নেই৷

Tagsadolescence age of consent age of marriage caa child marriage corona and nursing covid19 Covid impacts on education domestic violence early marriage education during lockdown foremothers gender discrimination gender identity gender in school honour killing human rights intercommunity marriage interfaith marriage lockdown lockdown and economy lockdown and school education lockdown in india lockdown in school lockdown in schools love jihad marriage and legitimacy memoir of a nurse misogyny nrc nurse in bengal nursing nursing and gender discrimination nursing in bengal nursing in india online class online classes during lockdown online education right to choose partner school education during lockdown social taboo toxic masculinity transgender Women womens rights
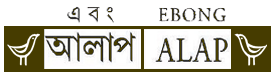
Leave a Reply